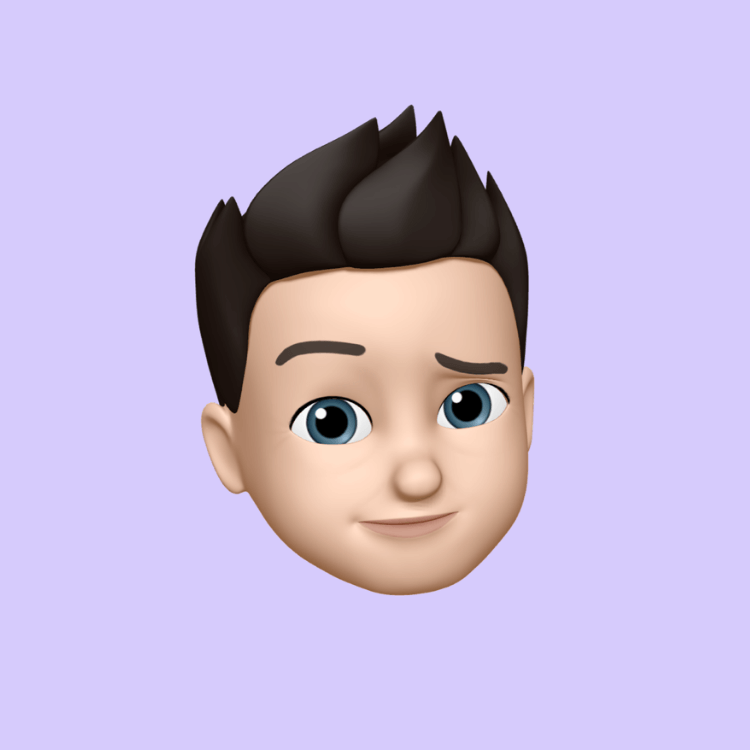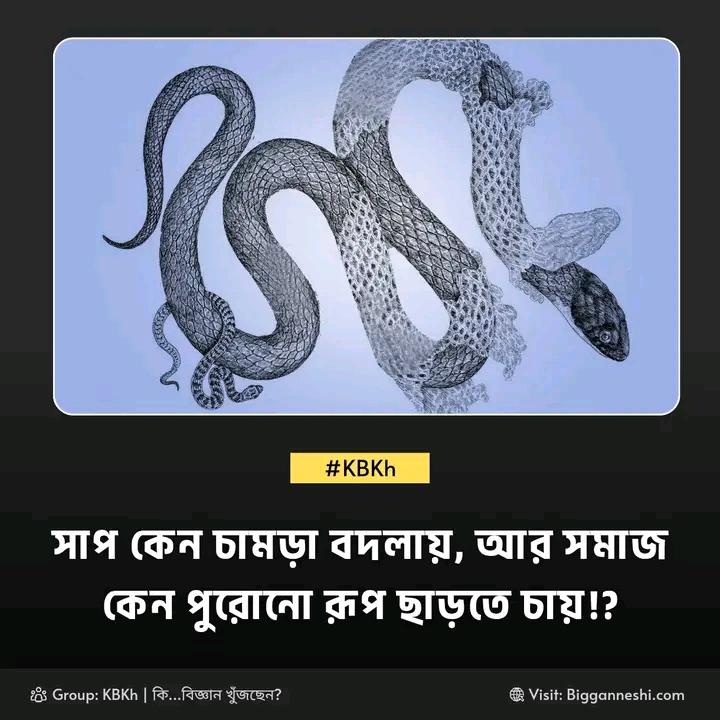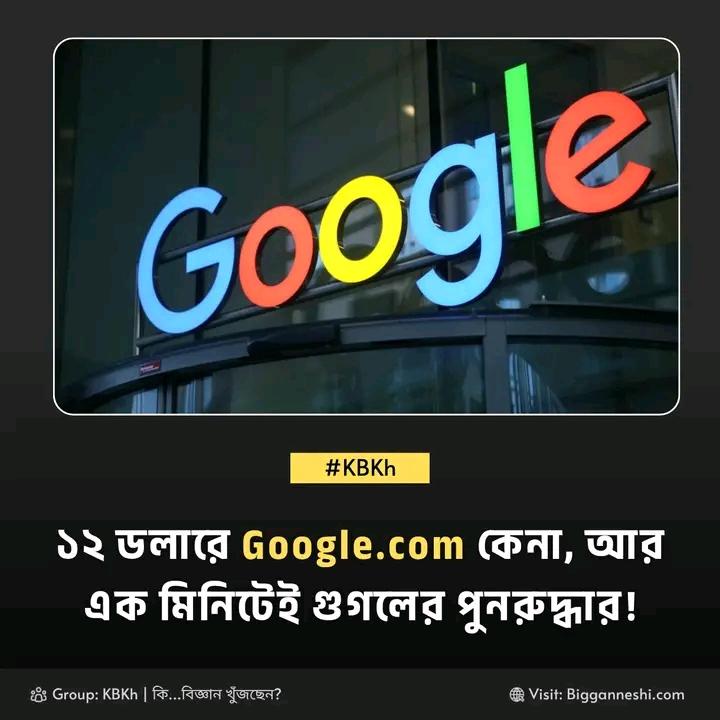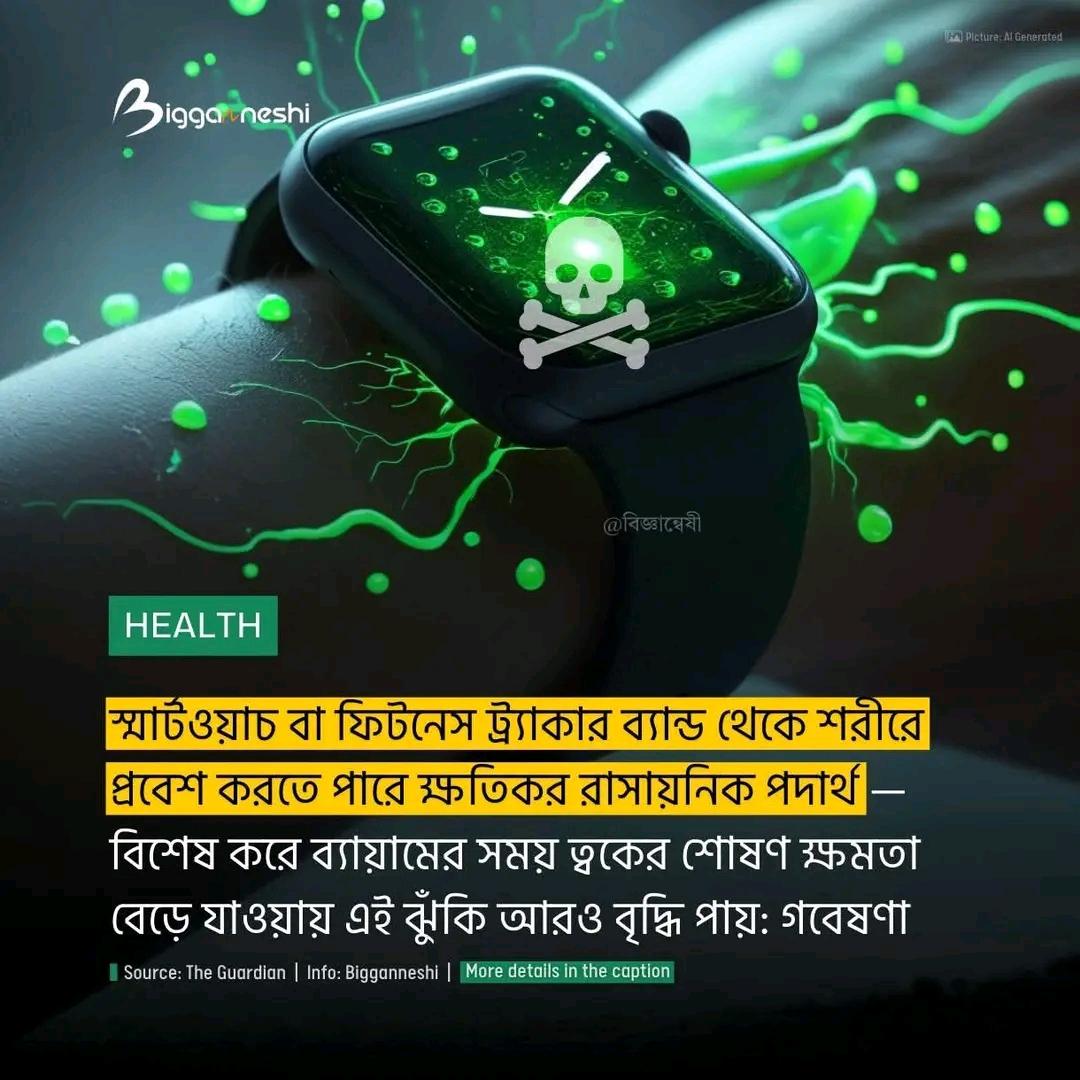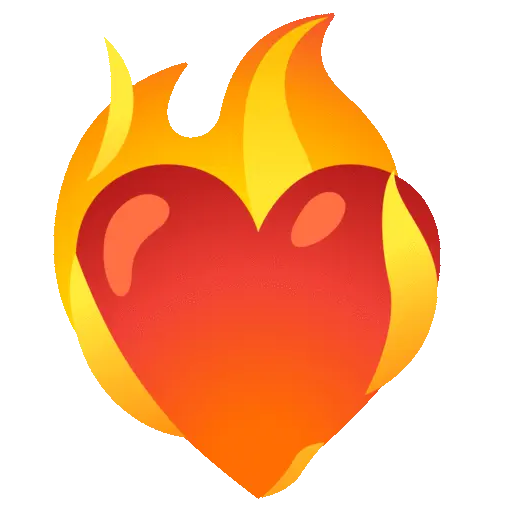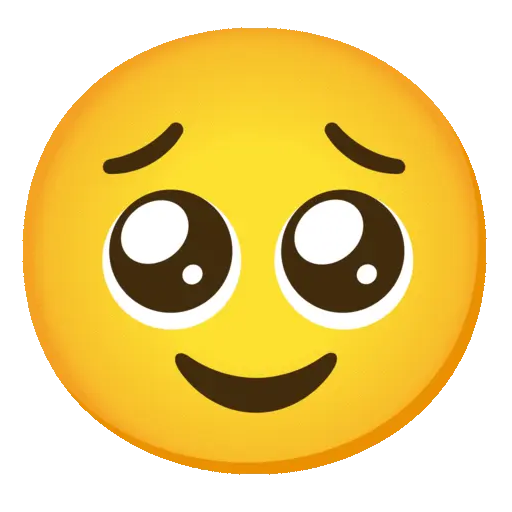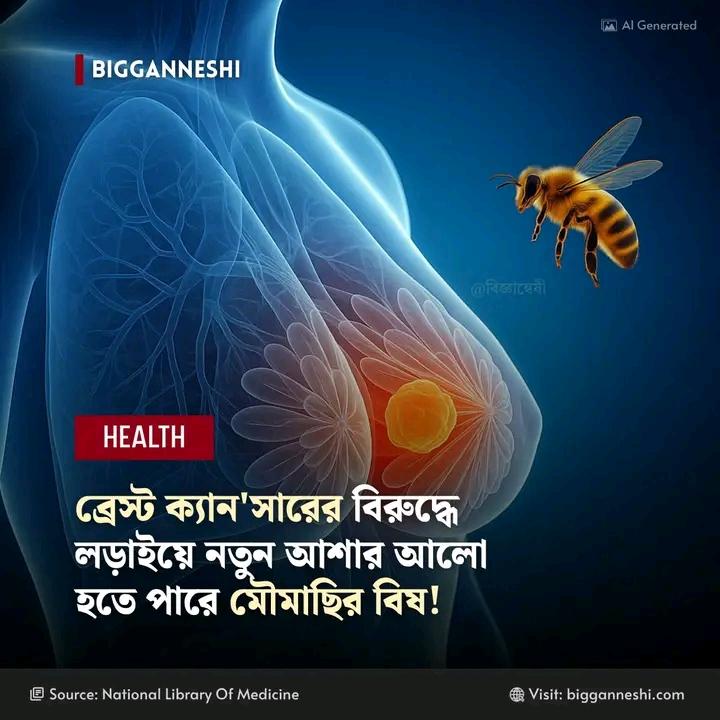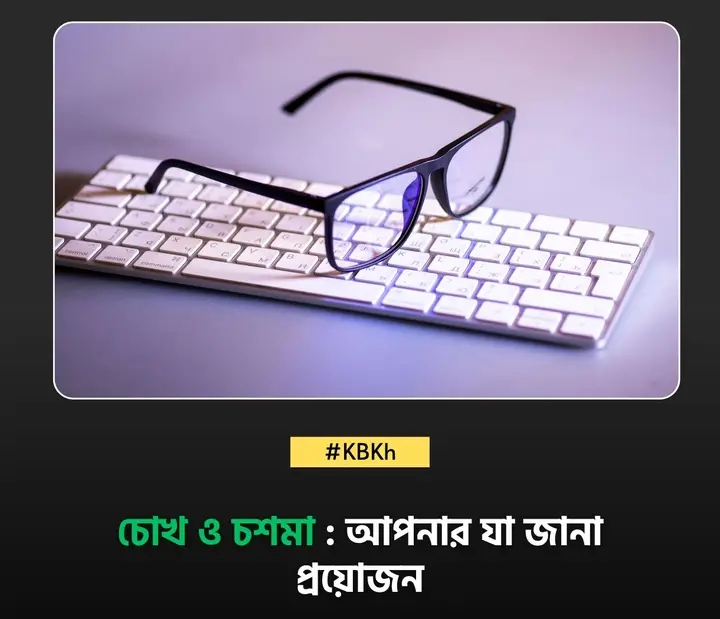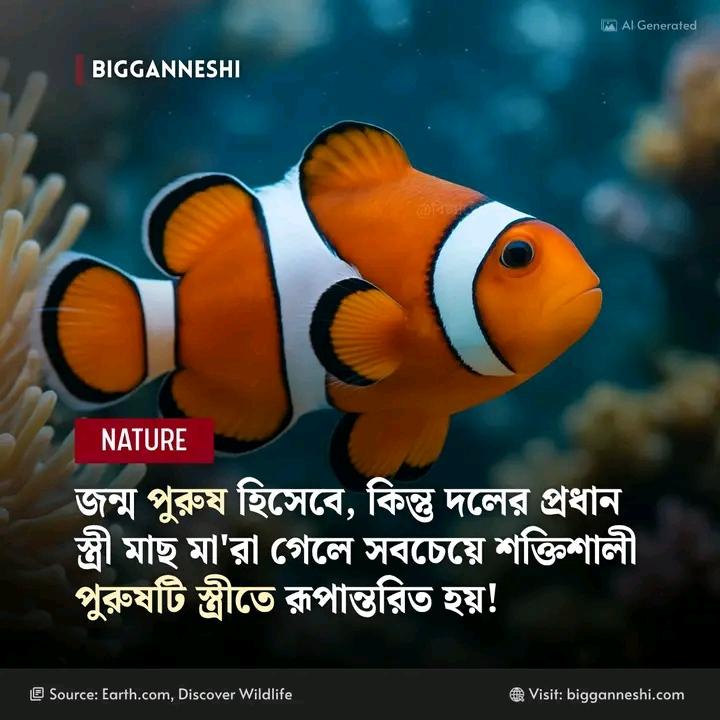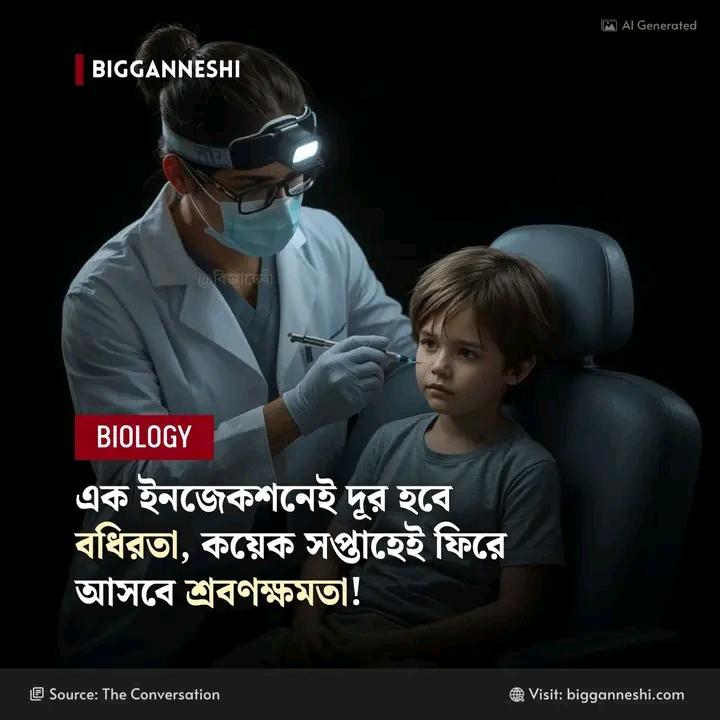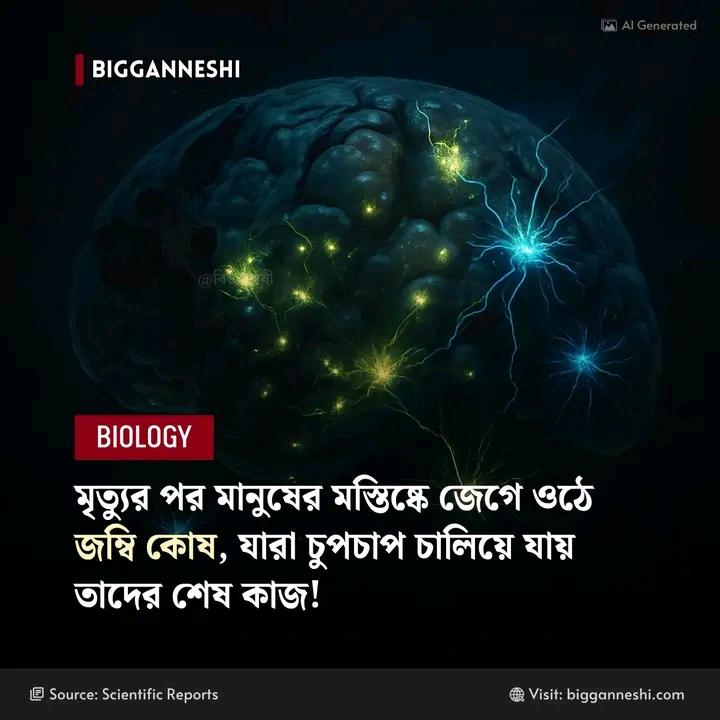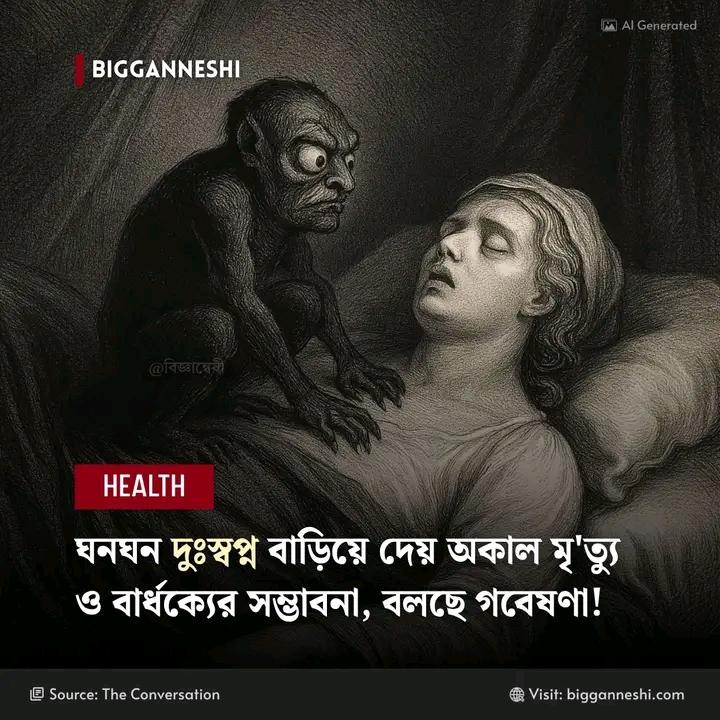আপনি কি কখনও খেয়াল করেছেন, সাপ তার নিজের চামড়া ফেলে দেয়? এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। বরং এটি তার জীবনের একটি স্বাভাবিক ও দরকারি অংশ। সাপের চামড়া বদলানো বা যাকে বলে molting বা ecdysis, তা কেবল একটা শারীরিক প্রক্রিয়া নয়। এতে লুকিয়ে আছে এক গভীর বার্তা, যেটা শুধু প্রাণিবিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ছড়িয়ে পড়ে সমাজ, সংস্কৃতি আর মানুষের মনোজগত পর্যন্ত।
সাপের শরীর যখন বাড়তে থাকে, তখন তার পুরনো চামড়া আর সহ্য করতে পারে না সেই বিস্তৃতি। সেটা আঁটসাঁট হয়ে যায়, দাগ পড়ে, আর কখনও কখনও হয়তো ক্ষতও তৈরি হয়। এই পুরনো আবরণ তখন আর কাজে আসে না। সাপ তখন ধীরে ধীরে গা ঘেঁষে, গাছের গুঁড়িতে ঘষে বা মাটির খোঁচায় ফেলে দেয় সেই পুরনো চামড়া। তার নিচে থাকে একেবারে নতুন, উজ্জ্বল আর সতেজ একটি আবরণ।
এখন আপনি ভাবতে পারেন, প্রাণীজগতের এই স্বাভাবিক বিষয় আমাদের সমাজের সঙ্গে কেমন করে মিলে যায়? এখানেই আসল কথাটা। প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি রাষ্ট্র বা জাতিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, সেই বদলটা বাধা পায় পুরনো কাঠামো, পুরনো চিন্তা আর পুরনো অভ্যাসে। যেমন পুরনো চামড়া সাপের শরীরকে আটকে রাখে, তেমনই পুরনো পদ্ধতি কোনো একটি জাতিকে আটকে রাখে তার সম্ভাবনার পথে।
একটা সময় আসে, যখন সেই জাতির সাধারণ মানুষ অনুভব করে যে তারা আর আগের মতো থাকতে পারছে না। চারপাশে অন্যায়, অবিচার, অন্যরকম চাপ যেন তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে তুলেছে। তখনই শুরু হয় মনোজাগতিক চাপ, যেটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ে সামাজিক প্রতিক্রিয়ায়। পুরনো শাসনব্যবস্থা, কর্তৃত্ববাদ, দুর্নীতি কিংবা মিথ্যার চাদর আর ধরা থাকে না। মানুষ তখন সেই চামড়া ছাড়তে চায়। যেটা এখন আর মানানসই নয়, যেটা গলা টিপে ধরেছে, সেটা তারা সরিয়ে ফেলতে চায়।
আপনি যদি ভেবে দেখেন, তাহলে বুঝবেন এই পরিবর্তনও একধরনের molting। শুধু পার্থক্য হলো, এখানে রক্তমাংসের চামড়া নয়, বদলায় চিন্তা, বদলায় মূল্যবোধ, বদলায় নেতৃত্ব আর সমাজের চালচিত্র। এই বদল সহজে আসে না, কারণ পুরনো কিছু শক্তি সবসময়ই আঁকড়ে থাকতে চায় সেই পুরনো অবস্থান। কিন্তু ঠিক যেমন সাপ চাইলেই তার চামড়া ধরে রাখতে পারে না, তেমনি একসময় সমাজও আর আগের রূপে থাকতে পারে না। সময় তাকে বদলে দেয়।
এখানে বিজ্ঞানের একটা দারুণ ব্যাখ্যা আছে। প্রাণীজগতে ecdysis হলো টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। কারণ পুরনো চামড়া ধরে রাখলে সাপ অসুস্থ হয়ে পড়ে, চলাফেরা করতে পারে না, এমনকি মা-রা যেতে পারে। সমাজেও একই নিয়ম চলে। পরিবর্তনের দরজা বন্ধ থাকলে সেখানে এক ধরনের পচন শুরু হয়। মানুষ অসন্তুষ্ট হয়, মনের ভেতর জমতে থাকে ক্ষোভ আর হতাশা। এসব একসময় বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই বিস্ফোরণ হয়তো একদিনে আসে না, কিন্তু আসে ঠিক তখনই, যখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় থাকে না।
আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন এমন উদাহরণ অসংখ্য। ছোট-বড় সব সমাজেই সময় এসে গেছে যখন মানুষ বলেছে, এভাবে আর চলবে না। তারা নতুন কিছু চেয়েছে, একটা সতেজ শ্বাস নিতে চেয়েছে। সেই চাওয়াটাই হয় সমাজের নতুন চামড়া। আর যারা পুরনোটা আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা একসময় হারিয়ে যায়।
তাই, সাপের এই চামড়া বদলের ঘটনা শুধু প্রকৃতির একটা বিস্ময় নয়, এটা আমাদের জন্য এক শিক্ষাও। আপনার সমাজ, আপনার দেশ, এমনকি আপনার নিজের জীবনও হয়তো এমন এক পর্যায়ে আছে যেখানে পুরনো কিছু ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। প্রশ্ন হলো, আপনি সেটা অনুভব করতে পারছেন কি না।
Join: KBKh | Bigganneshi - বিজ্ঞান্বেষী
সাপের শরীর যখন বাড়তে থাকে, তখন তার পুরনো চামড়া আর সহ্য করতে পারে না সেই বিস্তৃতি। সেটা আঁটসাঁট হয়ে যায়, দাগ পড়ে, আর কখনও কখনও হয়তো ক্ষতও তৈরি হয়। এই পুরনো আবরণ তখন আর কাজে আসে না। সাপ তখন ধীরে ধীরে গা ঘেঁষে, গাছের গুঁড়িতে ঘষে বা মাটির খোঁচায় ফেলে দেয় সেই পুরনো চামড়া। তার নিচে থাকে একেবারে নতুন, উজ্জ্বল আর সতেজ একটি আবরণ।
এখন আপনি ভাবতে পারেন, প্রাণীজগতের এই স্বাভাবিক বিষয় আমাদের সমাজের সঙ্গে কেমন করে মিলে যায়? এখানেই আসল কথাটা। প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি রাষ্ট্র বা জাতিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, সেই বদলটা বাধা পায় পুরনো কাঠামো, পুরনো চিন্তা আর পুরনো অভ্যাসে। যেমন পুরনো চামড়া সাপের শরীরকে আটকে রাখে, তেমনই পুরনো পদ্ধতি কোনো একটি জাতিকে আটকে রাখে তার সম্ভাবনার পথে।
একটা সময় আসে, যখন সেই জাতির সাধারণ মানুষ অনুভব করে যে তারা আর আগের মতো থাকতে পারছে না। চারপাশে অন্যায়, অবিচার, অন্যরকম চাপ যেন তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে তুলেছে। তখনই শুরু হয় মনোজাগতিক চাপ, যেটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ে সামাজিক প্রতিক্রিয়ায়। পুরনো শাসনব্যবস্থা, কর্তৃত্ববাদ, দুর্নীতি কিংবা মিথ্যার চাদর আর ধরা থাকে না। মানুষ তখন সেই চামড়া ছাড়তে চায়। যেটা এখন আর মানানসই নয়, যেটা গলা টিপে ধরেছে, সেটা তারা সরিয়ে ফেলতে চায়।
আপনি যদি ভেবে দেখেন, তাহলে বুঝবেন এই পরিবর্তনও একধরনের molting। শুধু পার্থক্য হলো, এখানে রক্তমাংসের চামড়া নয়, বদলায় চিন্তা, বদলায় মূল্যবোধ, বদলায় নেতৃত্ব আর সমাজের চালচিত্র। এই বদল সহজে আসে না, কারণ পুরনো কিছু শক্তি সবসময়ই আঁকড়ে থাকতে চায় সেই পুরনো অবস্থান। কিন্তু ঠিক যেমন সাপ চাইলেই তার চামড়া ধরে রাখতে পারে না, তেমনি একসময় সমাজও আর আগের রূপে থাকতে পারে না। সময় তাকে বদলে দেয়।
এখানে বিজ্ঞানের একটা দারুণ ব্যাখ্যা আছে। প্রাণীজগতে ecdysis হলো টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। কারণ পুরনো চামড়া ধরে রাখলে সাপ অসুস্থ হয়ে পড়ে, চলাফেরা করতে পারে না, এমনকি মা-রা যেতে পারে। সমাজেও একই নিয়ম চলে। পরিবর্তনের দরজা বন্ধ থাকলে সেখানে এক ধরনের পচন শুরু হয়। মানুষ অসন্তুষ্ট হয়, মনের ভেতর জমতে থাকে ক্ষোভ আর হতাশা। এসব একসময় বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই বিস্ফোরণ হয়তো একদিনে আসে না, কিন্তু আসে ঠিক তখনই, যখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় থাকে না।
আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন এমন উদাহরণ অসংখ্য। ছোট-বড় সব সমাজেই সময় এসে গেছে যখন মানুষ বলেছে, এভাবে আর চলবে না। তারা নতুন কিছু চেয়েছে, একটা সতেজ শ্বাস নিতে চেয়েছে। সেই চাওয়াটাই হয় সমাজের নতুন চামড়া। আর যারা পুরনোটা আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা একসময় হারিয়ে যায়।
তাই, সাপের এই চামড়া বদলের ঘটনা শুধু প্রকৃতির একটা বিস্ময় নয়, এটা আমাদের জন্য এক শিক্ষাও। আপনার সমাজ, আপনার দেশ, এমনকি আপনার নিজের জীবনও হয়তো এমন এক পর্যায়ে আছে যেখানে পুরনো কিছু ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। প্রশ্ন হলো, আপনি সেটা অনুভব করতে পারছেন কি না।
Join: KBKh | Bigganneshi - বিজ্ঞান্বেষী
আপনি কি কখনও খেয়াল করেছেন, সাপ তার নিজের চামড়া ফেলে দেয়? এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। বরং এটি তার জীবনের একটি স্বাভাবিক ও দরকারি অংশ। সাপের চামড়া বদলানো বা যাকে বলে molting বা ecdysis, তা কেবল একটা শারীরিক প্রক্রিয়া নয়। এতে লুকিয়ে আছে এক গভীর বার্তা, যেটা শুধু প্রাণিবিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ছড়িয়ে পড়ে সমাজ, সংস্কৃতি আর মানুষের মনোজগত পর্যন্ত।
সাপের শরীর যখন বাড়তে থাকে, তখন তার পুরনো চামড়া আর সহ্য করতে পারে না সেই বিস্তৃতি। সেটা আঁটসাঁট হয়ে যায়, দাগ পড়ে, আর কখনও কখনও হয়তো ক্ষতও তৈরি হয়। এই পুরনো আবরণ তখন আর কাজে আসে না। সাপ তখন ধীরে ধীরে গা ঘেঁষে, গাছের গুঁড়িতে ঘষে বা মাটির খোঁচায় ফেলে দেয় সেই পুরনো চামড়া। তার নিচে থাকে একেবারে নতুন, উজ্জ্বল আর সতেজ একটি আবরণ।
এখন আপনি ভাবতে পারেন, প্রাণীজগতের এই স্বাভাবিক বিষয় আমাদের সমাজের সঙ্গে কেমন করে মিলে যায়? এখানেই আসল কথাটা। প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি রাষ্ট্র বা জাতিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, সেই বদলটা বাধা পায় পুরনো কাঠামো, পুরনো চিন্তা আর পুরনো অভ্যাসে। যেমন পুরনো চামড়া সাপের শরীরকে আটকে রাখে, তেমনই পুরনো পদ্ধতি কোনো একটি জাতিকে আটকে রাখে তার সম্ভাবনার পথে।
একটা সময় আসে, যখন সেই জাতির সাধারণ মানুষ অনুভব করে যে তারা আর আগের মতো থাকতে পারছে না। চারপাশে অন্যায়, অবিচার, অন্যরকম চাপ যেন তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে তুলেছে। তখনই শুরু হয় মনোজাগতিক চাপ, যেটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ে সামাজিক প্রতিক্রিয়ায়। পুরনো শাসনব্যবস্থা, কর্তৃত্ববাদ, দুর্নীতি কিংবা মিথ্যার চাদর আর ধরা থাকে না। মানুষ তখন সেই চামড়া ছাড়তে চায়। যেটা এখন আর মানানসই নয়, যেটা গলা টিপে ধরেছে, সেটা তারা সরিয়ে ফেলতে চায়।
আপনি যদি ভেবে দেখেন, তাহলে বুঝবেন এই পরিবর্তনও একধরনের molting। শুধু পার্থক্য হলো, এখানে রক্তমাংসের চামড়া নয়, বদলায় চিন্তা, বদলায় মূল্যবোধ, বদলায় নেতৃত্ব আর সমাজের চালচিত্র। এই বদল সহজে আসে না, কারণ পুরনো কিছু শক্তি সবসময়ই আঁকড়ে থাকতে চায় সেই পুরনো অবস্থান। কিন্তু ঠিক যেমন সাপ চাইলেই তার চামড়া ধরে রাখতে পারে না, তেমনি একসময় সমাজও আর আগের রূপে থাকতে পারে না। সময় তাকে বদলে দেয়।
এখানে বিজ্ঞানের একটা দারুণ ব্যাখ্যা আছে। প্রাণীজগতে ecdysis হলো টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। কারণ পুরনো চামড়া ধরে রাখলে সাপ অসুস্থ হয়ে পড়ে, চলাফেরা করতে পারে না, এমনকি মা-রা যেতে পারে। সমাজেও একই নিয়ম চলে। পরিবর্তনের দরজা বন্ধ থাকলে সেখানে এক ধরনের পচন শুরু হয়। মানুষ অসন্তুষ্ট হয়, মনের ভেতর জমতে থাকে ক্ষোভ আর হতাশা। এসব একসময় বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই বিস্ফোরণ হয়তো একদিনে আসে না, কিন্তু আসে ঠিক তখনই, যখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় থাকে না।
আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন এমন উদাহরণ অসংখ্য। ছোট-বড় সব সমাজেই সময় এসে গেছে যখন মানুষ বলেছে, এভাবে আর চলবে না। তারা নতুন কিছু চেয়েছে, একটা সতেজ শ্বাস নিতে চেয়েছে। সেই চাওয়াটাই হয় সমাজের নতুন চামড়া। আর যারা পুরনোটা আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা একসময় হারিয়ে যায়।
তাই, সাপের এই চামড়া বদলের ঘটনা শুধু প্রকৃতির একটা বিস্ময় নয়, এটা আমাদের জন্য এক শিক্ষাও। আপনার সমাজ, আপনার দেশ, এমনকি আপনার নিজের জীবনও হয়তো এমন এক পর্যায়ে আছে যেখানে পুরনো কিছু ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। প্রশ্ন হলো, আপনি সেটা অনুভব করতে পারছেন কি না।
Join: KBKh | Bigganneshi - বিজ্ঞান্বেষী
0 Commentaires
0 Parts
542 Vue