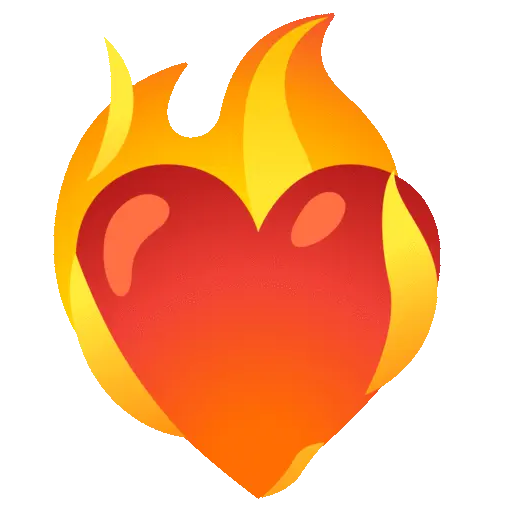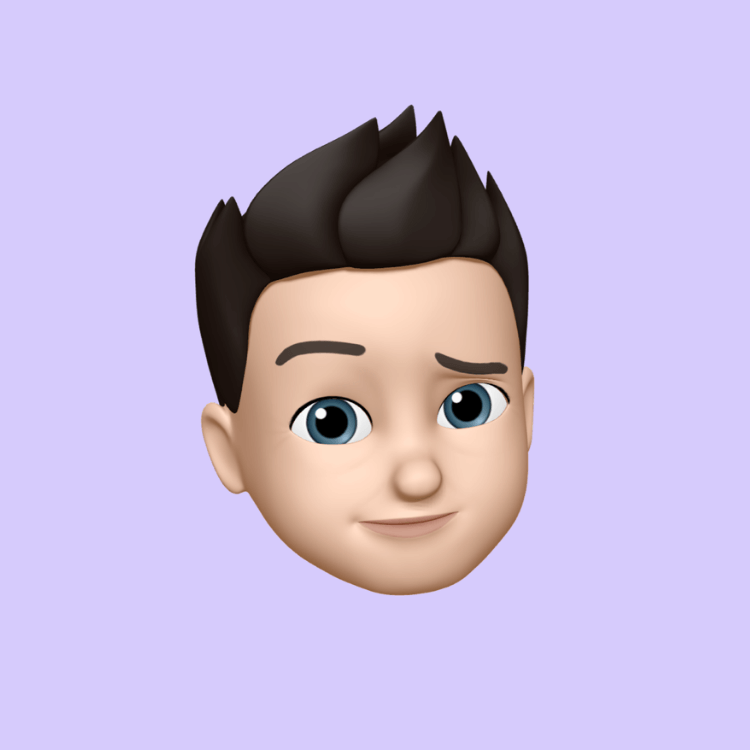বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে সবচেয়ে বড় বাটপারিটা কোথায় জানেন? আমাদের শিক্ষার্থীরা সত্যিকারের শিক্ষক খুব কম পেয়েছে। আসলে শিক্ষক নিয়োগই দেওয়া হয় না। শিক্ষক নিয়োগ হবে কিভাবে? শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা কি সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালার সাথে যায়? সত্যিকারের মেধাবীরা কি বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চায়? আগে দেশে বা বিদেশে সুযোগ কম ছিল বলে আমাদের হারুন স্যার, আমাদের আহমেদ শফী স্যার, আমাদের কবির স্যারদের শিক্ষকরা বিদেশে না থেকে দেশে ফিরে এসেছিল। আরেকটা কারণ ছিল তাদের অধিকাংশই আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের ছিলেন। ইন ফ্যাক্ট, আগের শিক্ষকদের পরিবারের খোঁজ খবর নিয়ে দেখলে দেখবেন প্রায় সবাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছিলেন। তাছাড়া তখন শিক্ষকতা পেশায় বেতন কম হলেও সমাজে মর্যাদা ছিল। এখন অধিকাংশ শিক্ষকই এসেছেন অস্বচ্ছল পরিবার থেকে। কারণ স্বচ্ছল উচ্চবিত্তের ছেলেমেয়েরা এখন আর তেমন বাংলা মাধ্যমে পড়ে না। তারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে বিদেশে চলে যায় যাদের অধিকাংশই আর দেশে ফিরে না।
দেখা যায় বাংলা মাধ্যমে পড়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরা। এরাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। তাদের মধ্যেও যারা মেধাবী এখন তারাও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেই না। মাস্টার্স এমনকি অনার্স পাশ করেই এখন মেধাবীদের একটা বড় অংশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যাচ্ছে। আর গিয়ে প্রায় সবাই সেখানে থেকে যাচ্ছে। ফলে মধ্যবিত্তের মধ্যেও গড়ে অপেক্ষাকৃত একটু কম মেধাবীদেরই আমরা শিক্ষক হিসাবে পাচ্ছি। আবার এই মধ্যবিত্ত ক্লাসের ছেলেমেয়েদের থেকেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার বাসনা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি, আবাসিক হলগুলোতে টর্চার, মিছিল মিটিং-এ নেয়ার চাপ, সেশন জ্যাম ইত্যাদিসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই ঢাকা শহরে নামিদামি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক মেধাবী শিক্ষক আছে। পদার্থবিজ্ঞানে যারা খুবই মেধাবী তাদের অনেকের সাথেই আমার সখ্যতা আছে। আলাপে আলাপে জিজ্ঞেস করি তারা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক কিনা। কোন প্রকার দ্বিধা দন্দ্ব ছাড়া তাদের উত্তর "না"! এমন কি গত কয়েক বছরে আমাদের অনেক মেধাবী শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছে। এইসব নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কোন রকম চিন্তা আছে? একটু অসচ্ছল ও নিম্নবিত্ত থেকে আসার কারণে অধিকাংশ শিক্ষকই পার্ট-টাইম অন্যত্র পড়ায়। পড়াবে না কেন? সরকারি অন্যান্য চাকুরীতে বেতনের বাহিরে গাড়ি পায়, ড্রাইভার পায়, গাড়ির তেল পায়, সুদবিহীন লোন পায়, বাসা পায়, প্রতি মিটিং-এ সিটিং মানি পায়, বিদেশে ট্রেনিং এর নামে অনেক সুবিধা পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কি পায়?
এইটা কাঙ্খিত যে ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবীরা শিক্ষার্থী শিক্ষক হবে? প্রভাষকের বেতন কত? ৩০-৩৫ হাজার! সহকারী অধ্যাপকের বেতন কত? বড়জোর ৪০-৪৫ হাজার টাকা। অথচ অধিকাংশ সহকারী অধ্যাপকের পিএইচডি পর্যন্ত থাকে। সেই পিএইচডিও রাষ্ট্রের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় নয় বরং স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ পেয়ে পিএইচডি করা। এই মেধাবীদের কি আমরা মূল্যায়ন করছি? এরপর আমাদের মেধাবীরা পিএইচডি শেষে ফিরে আসলেও রাজনীতির কারণে তাদের নিয়োগ হবে না। দেখা হবে প্রার্থীর বাবা, দাদা নানা কোন রাজনীতি করতো? চাকুরীর জন্য সুপারশি করার জন্য প্রার্থীর কোন গড ফাদার আছে কিনা। এইসব নানা কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা আসলে যাদের শিক্ষক হিসাবে পাচ্ছে তাদের একটা বড় অংশ আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ারই কথা না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে এখন ন্যূনতম যোগ্যতা পিএইচডি যথেষ্ট না। সাথে থাকতে হয় পোস্ট-ডক। শুধু পিএইচডি থাকলে তাকে প্রমান করতে হয় তার যোগ্যতা। পিএইচডি ও পোস্ট-ডক শেষে যিনি নিয়োগ পায় তার বয়স ন্যূনতম ৩০-৩৫ বা তার বেশি। এত কিছু করার কারণে সে অলরেডি matured! এইরকম শিক্ষকদের যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব অন্যরকম হয়। এইরকম শিক্ষকদের দেখলে শিক্ষার্থীরা সম্মান করবে। আমরাতো আসলে সত্যিকারের শিক্ষক নিয়োগই দেইনি। বিশাল সংখ্যক অশিক্ষকদের শিক্ষক হিসাবে পেয়ে সমাজ এবং শিক্কার্থীদের মাঝে শিক্ষক সম্মন্ধে খারাপ ধারণা জন্মেছে। এই ধারণা নিয়ে ক্লাসে গেলে কদাচিৎ কেউ ভালো পড়ালেও শিক্ষার্থীরা ভেবে নেয় অন্যদের মতোই। ক্লাসে মনোযোগ দেয় না। এইভাবেই আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে নষ্ট করে ফেলছি।
@highlight
দেখা যায় বাংলা মাধ্যমে পড়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরা। এরাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। তাদের মধ্যেও যারা মেধাবী এখন তারাও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেই না। মাস্টার্স এমনকি অনার্স পাশ করেই এখন মেধাবীদের একটা বড় অংশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যাচ্ছে। আর গিয়ে প্রায় সবাই সেখানে থেকে যাচ্ছে। ফলে মধ্যবিত্তের মধ্যেও গড়ে অপেক্ষাকৃত একটু কম মেধাবীদেরই আমরা শিক্ষক হিসাবে পাচ্ছি। আবার এই মধ্যবিত্ত ক্লাসের ছেলেমেয়েদের থেকেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার বাসনা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি, আবাসিক হলগুলোতে টর্চার, মিছিল মিটিং-এ নেয়ার চাপ, সেশন জ্যাম ইত্যাদিসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই ঢাকা শহরে নামিদামি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক মেধাবী শিক্ষক আছে। পদার্থবিজ্ঞানে যারা খুবই মেধাবী তাদের অনেকের সাথেই আমার সখ্যতা আছে। আলাপে আলাপে জিজ্ঞেস করি তারা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক কিনা। কোন প্রকার দ্বিধা দন্দ্ব ছাড়া তাদের উত্তর "না"! এমন কি গত কয়েক বছরে আমাদের অনেক মেধাবী শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছে। এইসব নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কোন রকম চিন্তা আছে? একটু অসচ্ছল ও নিম্নবিত্ত থেকে আসার কারণে অধিকাংশ শিক্ষকই পার্ট-টাইম অন্যত্র পড়ায়। পড়াবে না কেন? সরকারি অন্যান্য চাকুরীতে বেতনের বাহিরে গাড়ি পায়, ড্রাইভার পায়, গাড়ির তেল পায়, সুদবিহীন লোন পায়, বাসা পায়, প্রতি মিটিং-এ সিটিং মানি পায়, বিদেশে ট্রেনিং এর নামে অনেক সুবিধা পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কি পায়?
এইটা কাঙ্খিত যে ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবীরা শিক্ষার্থী শিক্ষক হবে? প্রভাষকের বেতন কত? ৩০-৩৫ হাজার! সহকারী অধ্যাপকের বেতন কত? বড়জোর ৪০-৪৫ হাজার টাকা। অথচ অধিকাংশ সহকারী অধ্যাপকের পিএইচডি পর্যন্ত থাকে। সেই পিএইচডিও রাষ্ট্রের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় নয় বরং স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ পেয়ে পিএইচডি করা। এই মেধাবীদের কি আমরা মূল্যায়ন করছি? এরপর আমাদের মেধাবীরা পিএইচডি শেষে ফিরে আসলেও রাজনীতির কারণে তাদের নিয়োগ হবে না। দেখা হবে প্রার্থীর বাবা, দাদা নানা কোন রাজনীতি করতো? চাকুরীর জন্য সুপারশি করার জন্য প্রার্থীর কোন গড ফাদার আছে কিনা। এইসব নানা কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা আসলে যাদের শিক্ষক হিসাবে পাচ্ছে তাদের একটা বড় অংশ আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ারই কথা না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে এখন ন্যূনতম যোগ্যতা পিএইচডি যথেষ্ট না। সাথে থাকতে হয় পোস্ট-ডক। শুধু পিএইচডি থাকলে তাকে প্রমান করতে হয় তার যোগ্যতা। পিএইচডি ও পোস্ট-ডক শেষে যিনি নিয়োগ পায় তার বয়স ন্যূনতম ৩০-৩৫ বা তার বেশি। এত কিছু করার কারণে সে অলরেডি matured! এইরকম শিক্ষকদের যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব অন্যরকম হয়। এইরকম শিক্ষকদের দেখলে শিক্ষার্থীরা সম্মান করবে। আমরাতো আসলে সত্যিকারের শিক্ষক নিয়োগই দেইনি। বিশাল সংখ্যক অশিক্ষকদের শিক্ষক হিসাবে পেয়ে সমাজ এবং শিক্কার্থীদের মাঝে শিক্ষক সম্মন্ধে খারাপ ধারণা জন্মেছে। এই ধারণা নিয়ে ক্লাসে গেলে কদাচিৎ কেউ ভালো পড়ালেও শিক্ষার্থীরা ভেবে নেয় অন্যদের মতোই। ক্লাসে মনোযোগ দেয় না। এইভাবেই আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে নষ্ট করে ফেলছি।
@highlight
বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে সবচেয়ে বড় বাটপারিটা কোথায় জানেন? আমাদের শিক্ষার্থীরা সত্যিকারের শিক্ষক খুব কম পেয়েছে। আসলে শিক্ষক নিয়োগই দেওয়া হয় না। শিক্ষক নিয়োগ হবে কিভাবে? শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা কি সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালার সাথে যায়? সত্যিকারের মেধাবীরা কি বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চায়? আগে দেশে বা বিদেশে সুযোগ কম ছিল বলে আমাদের হারুন স্যার, আমাদের আহমেদ শফী স্যার, আমাদের কবির স্যারদের শিক্ষকরা বিদেশে না থেকে দেশে ফিরে এসেছিল। আরেকটা কারণ ছিল তাদের অধিকাংশই আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের ছিলেন। ইন ফ্যাক্ট, আগের শিক্ষকদের পরিবারের খোঁজ খবর নিয়ে দেখলে দেখবেন প্রায় সবাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছিলেন। তাছাড়া তখন শিক্ষকতা পেশায় বেতন কম হলেও সমাজে মর্যাদা ছিল। এখন অধিকাংশ শিক্ষকই এসেছেন অস্বচ্ছল পরিবার থেকে। কারণ স্বচ্ছল উচ্চবিত্তের ছেলেমেয়েরা এখন আর তেমন বাংলা মাধ্যমে পড়ে না। তারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে বিদেশে চলে যায় যাদের অধিকাংশই আর দেশে ফিরে না।
দেখা যায় বাংলা মাধ্যমে পড়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরা। এরাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে। তাদের মধ্যেও যারা মেধাবী এখন তারাও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেই না। মাস্টার্স এমনকি অনার্স পাশ করেই এখন মেধাবীদের একটা বড় অংশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যাচ্ছে। আর গিয়ে প্রায় সবাই সেখানে থেকে যাচ্ছে। ফলে মধ্যবিত্তের মধ্যেও গড়ে অপেক্ষাকৃত একটু কম মেধাবীদেরই আমরা শিক্ষক হিসাবে পাচ্ছি। আবার এই মধ্যবিত্ত ক্লাসের ছেলেমেয়েদের থেকেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার বাসনা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক রাজনীতি, আবাসিক হলগুলোতে টর্চার, মিছিল মিটিং-এ নেয়ার চাপ, সেশন জ্যাম ইত্যাদিসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই ঢাকা শহরে নামিদামি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক মেধাবী শিক্ষক আছে। পদার্থবিজ্ঞানে যারা খুবই মেধাবী তাদের অনেকের সাথেই আমার সখ্যতা আছে। আলাপে আলাপে জিজ্ঞেস করি তারা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক কিনা। কোন প্রকার দ্বিধা দন্দ্ব ছাড়া তাদের উত্তর "না"! এমন কি গত কয়েক বছরে আমাদের অনেক মেধাবী শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছে। এইসব নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কোন রকম চিন্তা আছে? একটু অসচ্ছল ও নিম্নবিত্ত থেকে আসার কারণে অধিকাংশ শিক্ষকই পার্ট-টাইম অন্যত্র পড়ায়। পড়াবে না কেন? সরকারি অন্যান্য চাকুরীতে বেতনের বাহিরে গাড়ি পায়, ড্রাইভার পায়, গাড়ির তেল পায়, সুদবিহীন লোন পায়, বাসা পায়, প্রতি মিটিং-এ সিটিং মানি পায়, বিদেশে ট্রেনিং এর নামে অনেক সুবিধা পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কি পায়?
এইটা কাঙ্খিত যে ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবীরা শিক্ষার্থী শিক্ষক হবে? প্রভাষকের বেতন কত? ৩০-৩৫ হাজার! সহকারী অধ্যাপকের বেতন কত? বড়জোর ৪০-৪৫ হাজার টাকা। অথচ অধিকাংশ সহকারী অধ্যাপকের পিএইচডি পর্যন্ত থাকে। সেই পিএইচডিও রাষ্ট্রের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় নয় বরং স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ পেয়ে পিএইচডি করা। এই মেধাবীদের কি আমরা মূল্যায়ন করছি? এরপর আমাদের মেধাবীরা পিএইচডি শেষে ফিরে আসলেও রাজনীতির কারণে তাদের নিয়োগ হবে না। দেখা হবে প্রার্থীর বাবা, দাদা নানা কোন রাজনীতি করতো? চাকুরীর জন্য সুপারশি করার জন্য প্রার্থীর কোন গড ফাদার আছে কিনা। এইসব নানা কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা আসলে যাদের শিক্ষক হিসাবে পাচ্ছে তাদের একটা বড় অংশ আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ারই কথা না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে এখন ন্যূনতম যোগ্যতা পিএইচডি যথেষ্ট না। সাথে থাকতে হয় পোস্ট-ডক। শুধু পিএইচডি থাকলে তাকে প্রমান করতে হয় তার যোগ্যতা। পিএইচডি ও পোস্ট-ডক শেষে যিনি নিয়োগ পায় তার বয়স ন্যূনতম ৩০-৩৫ বা তার বেশি। এত কিছু করার কারণে সে অলরেডি matured! এইরকম শিক্ষকদের যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব অন্যরকম হয়। এইরকম শিক্ষকদের দেখলে শিক্ষার্থীরা সম্মান করবে। আমরাতো আসলে সত্যিকারের শিক্ষক নিয়োগই দেইনি। বিশাল সংখ্যক অশিক্ষকদের শিক্ষক হিসাবে পেয়ে সমাজ এবং শিক্কার্থীদের মাঝে শিক্ষক সম্মন্ধে খারাপ ধারণা জন্মেছে। এই ধারণা নিয়ে ক্লাসে গেলে কদাচিৎ কেউ ভালো পড়ালেও শিক্ষার্থীরা ভেবে নেয় অন্যদের মতোই। ক্লাসে মনোযোগ দেয় না। এইভাবেই আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে নষ্ট করে ফেলছি।
@highlight